মননশীলতা ও জীবনধারণের আদর্শিক বিশালতায় অন্নদাশঙ্কর রায়
(১৯০৪-২০০২) বিংশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজ ও জাতীয়-আন্তর্জাতিক মানবগোষ্ঠীর
সত্যানুসন্ধানী প্রাণপুরুষ।
আজ অন্নদাশঙ্কর রায়ের ১২১ তম জন্মদিন। ১৫ মার্চ, ১৯০৪ সালে
তিনি ভারতের উড়িষ্যা জেলার এক কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অন্নদাশঙ্কর দুই
বাংলার সাহিত্যিক। ভৌগোলিক সীমারেখায় তাঁকে বিচ্ছিন্ন করা মুশকিল। তাঁর জন্মদিনে
আরো বেশি প্রাসঙ্গিক তিনি ভারত-বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে। ঊনিশ শতকের বাঙালি রেনেসাঁ
ঐতিহ্যের শেষ বুদ্ধিজীবী হিসেবে তাঁর নামোচ্চারণ করা যায়। সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম
এমনকি জাতিকেন্দ্রিক ভাবনায় অন্নদাশঙ্কর রায়ের রেনেসাঁধর্মী যৌক্তিক বিশ্লেষণ ও
সংস্কারহীন অবস্থান তাঁকে উদার মানবতাবাদী করে তুলেছে। আবেগের চাইতে যুক্তিধর্মে
বিশ্বাসী এই সাহিত্যশিল্পীর মননের অন্তহীন কৌতুহল ও জিজ্ঞাসা তাঁর রচনাসম্ভারকে
করেছে কালোত্তীর্ণ।
অন্নদাশঙ্কর রায়ের সাহিত্যসৃষ্টি বৈচিত্র্যপূর্ণ। বাংলা গদ্য ও
পদ্যসাহিত্য উভয় শাখাতেই ছিলো তাঁর সমান পদচারণা। প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা,
ছড়া, ভ্রমণসাহিত্য ; সাহিত্যের প্রতিটি শাখাতে তাঁর অবস্থান ছিলো আদর্শিক ও
নিরপেক্ষ। তবে তাঁর সৃষ্টিসম্ভার বৃক্ষের প্রবন্ধ শাখাটি অন্যান্য সকল শাখাকে
যৌক্তিক দিক থেকে অতিক্রম করে গিয়েছে। রেনেসাঁ প্রাণিত উদার মানবতাবাদী
সাহিত্যশিল্পী হিসেবে তিনি তাঁর প্রবন্ধসাহিত্যের প্রতিটি শব্দ বুনেছেন বিজ্ঞানীর
দৃষ্টিকোণ থেকে। অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রবন্ধসাহিত্য সম্পর্কে অনেকেই বলে থাকেন,
তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্থক উত্তরসূরি। কিন্তু
আমি এই মতামতের সাথে সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করি৷ যুক্তি, প্রেম, বিবেক, স্বদেশ ও
বিশ্বচিন্তা এবং বিজ্ঞানমনস্কতার উপাদানসমূহের সমন্বয়ে বুঁনে যাওয়া প্রবন্ধসমূহের
প্রতিটি পঙ্ক্তিমালায় তাঁর অবস্থান ছিলো একান্নবর্তী চিন্তারহিত। নিজের বিরুদ্ধে
হলেও জীবন ও জগতের রূঢ় সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন তিনি তাঁর প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে।
পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজে বয়ে যাওয়া রেনেসাঁসের হিল্লোল অন্নদাশঙ্কর রায়ের সমস্ত চিন্তাজগকে করেছিলো আলোড়িত। প্রকৃত সাহিত্যশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার প্রথম সোপান হিসেবে তিনি যুক্তিনিষ্ঠার কঠিন সিঁড়ি ভাঙ্গার ব্যাপারে ছিলেন বদ্ধপরিকর। সমাজ, ধর্ম, ধর্ম ও রাষ্ট্র, সাহিত্য, সাহিত্য ব্যক্তিত্ত্ব, সংস্কৃতি ও মানবভাবনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি আলাদা আলাদা যৌক্তিক প্রশ্ন গেঁথে দিয়েছেন বাঙালির মননে। ‘রেনেসাঁ’, ‘বাংলার রেনেসাঁস: পুনর্ভাবনা’, ‘হিন্দু-মুসলমান’, ‘সেকুলার স্টেট’, ‘রাষ্ট্র বনাম নেশন’, ‘দেশপ্রেম বনাম জাতিপ্রেম’, ‘পশ্চিমা না আধুনিক’, ‘ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ’, ‘ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা’, ‘সংস্কৃতির সংকট’ ; প্রভৃতি প্রবন্ধসমূহে ধর্ম, রাষ্ট্র, সংস্কৃতি, মানবতাবাদ ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর বহুমাত্রিক সূক্ষ্ম যুক্তিবাদী জীবনবোধ আমাদেরকে আরেকবার বিষয়গুলো সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য করে।
অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রবন্ধসমূহের কিছু মৌল বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন:
ক. মানবিকতা,
খ. বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিবাদিতা,
গ. ধর্ম ও রাষ্ট্রকে আলাদা করে মানবমুক্তির পথের সন্ধান দেয়া,
ঘ. রাষ্ট্রভাবনায় অভিজাততন্ত্রের বিলোপ ও সাম্য প্রতিষ্ঠার
পক্ষে মত প্রকাশ,
ঙ. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার স্বীকৃতি, প্রভৃতি।
অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর দেশ ও জাতিভাবনাকেন্দ্রিক প্রবন্ধসমূহে সর্বদা অসাম্প্রদায়িকতা, উদার মানবিকতা, সাম্য এবং নাগরিকের অধিকারের প্রতি কলমের শাণিত শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন। সর্বত্র বলেছেন সমন্বয়ের কথা।
অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর রাষ্ট্রভাবনায় প্রজার কল্যাণার্থে
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ব্যক্ত করেছেন। 'সেকুলার স্টেট' প্রবন্ধে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ অর্থে সেক্যুলার স্টেটের ধারণাকে ভুল প্রমাণ করেছেন। বরং ধর্ম দ্বারা রাষ্ট্র
নিয়ন্ত্রিত হবে না এবং ‘প্রজাশক্তির অভ্যুদ্দয়’ হবে রাষ্ট্রের বুনিয়াদ ; এই সত্যকে
প্রতিষ্ঠিত করতে তৎপর ছিলেন তিনি৷ সারা ইউরোপ জুড়ে চার্চ বা ধর্ম প্রতিষ্ঠান থেকে
প্রটেস্ট্যান্ট দলের বেরিয়ে আসার বর্ণনা দিয়ে সমগ্র ভারত ও পূর্ববঙ্গে সেক্যুলার
স্টেট কামনা করেছেন৷ যার বাস্তবায়ন আমাদের বর্তমান যাপিত সময় ও সমাজে ভীষণভাবে
প্রয়োজন। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ অন্নদাশঙ্কর রায় মেনে নিতে পারেননি।
তাঁর প্রবন্ধে দেশভাগের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান ফুটে উঠেছে। ‘দেশপ্রেম বনাম
জাতিপ্রেম’ প্রবন্ধে আক্ষেপ করে বলেছেন, “আমাদের দেশপ্রেম খাঁটি ছিল বলে দেশ
স্বাধীন হল, কিন্তু আমাদের জাতিপ্রেমে খাদ ছিল, তাই দেশ খন্ডিত হল।.... বাহুবলের
দ্বারা দেশকে এক করতে পারা যায়, কিন্তু জাতিকে এক করা সম্ভব নয়। এর জন্য চাই
প্রেম।” সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ
প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তিনি ছিলেন সরব শব্দসৈনিক। ‘রাষ্ট্র বনাম নেশন’ প্রবন্ধে বলেছেন, “নেশন হয় স্বেচ্ছায়। রাষ্ট্র হয় গায়ের জোরে।” ইউরোপে ক্যাথলিক ও
প্রটেস্ট্যান্ট বিভেদ দূর করে এক জাতি গড়ার জন্য রাষ্ট্রগুলিকে যে ধর্মনিরপেক্ষ বা
সেক্যুলার স্টেট হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছিলো, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি বাঙালির দৃষ্টি
আকর্ষণ ছিলো তাঁর এই ধারার প্রবন্ধগুলির মূল উদ্দেশ্য। হিন্দু-মুসলিম হাজার বছর
একসাথে বাস করেও এক নেশন গড়তে না পারার ব্যর্থতার প্রতি ইঙ্গিত করে বাঙালির মরা
বিবেকবোধকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন তিনি।
ভারতবর্ষে রয়েছে এক বিমিশ্র ধর্মসভ্যতা।
মানবিক ও নৈতিক দায়বদ্ধ লেখক হিসেবে তিনি ভারতবর্ষের বিচিত্র
ধর্মের সহাবস্থানকে নিশ্চিত করতে চেয়েছেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। তার জবানীতে উঠে
এসেছে ভারতবর্ষে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিকাশের মূল কারণ। অবিভক্ত ভারতবর্ষে
মধ্যবিত্ত মুসলিম শ্রেণির বিকাশকে হিন্দুরা ভালোভাবে নেয়নি, যদি তারা এটা খুশি মনে
মেনে নিতো তাহলে হয়ত মুসলমানেরা দেশভাগের কথা মুখে আনত না। ‘হিন্দু-মুসলমান’ প্রবন্ধে তিনি বলেন, “মুসলমানকে ভারতের প্রয়োজন আছে। আমরা লক্ষ করেছি, যে
মানুষ হিন্দু থাকতে ‘দাস্য সুখে হাস্যমুখে বিনীত যোড়কর’ ছিল সেই মানুষ মুসলমান হয়ে ‘উন্নত মম শির’ বলে গান গেয়ে উঠেছে। সে তার আত্মার গান। যথার্থই তার কাছে ‘নতশির ঐ
শিখর হিমাদ্রির।’ “বিস্ময়ের বিষয় হলেও সত্য অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর প্রবন্ধে
হিন্দুদের ‘জাতিভেদ’ প্রথাকে সমর্থন করেছিলেন। তাঁর মতে, এতে বিভিন্ন শ্রেণির
মধ্যে বেকারত্বের সৃষ্টি হয়না। হিন্দুদের অযৌক্তিক গো-ভক্তির সমালোচনা করেছেন
তীব্র ভাষায়। তাঁর ধর্ম ছিলো মানবধর্ম। ‘সংস্কৃতির সংকট’ প্রবন্ধে দৃপ্তকণ্ঠে
উচ্চারণ করেন, “মানুষও ইচ্ছা করলে ও সাধনা করলে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান হতে
পারে। বিশ্বামিত্রের মতো নতুন জগৎ সৃষ্টি করতে পারে। সর্বগুণের সম্ভাব্যতা তার
ভিতরেই নিহিত রয়েছে। সে স্বর্গে যেতে চাইবেই বা কেন? স্বর্গ তো সে এই
মর্ত্যভূমিতেই গড়ে তুলতে পারে৷ এর জন্য একজন স্বর্গনিবাসী ঈশ্বরেরই বা কী দরকার?
খ্রিস্টধর্ম এসে গ্রিক, রোমান, টিউটনিক দেবদেবীকে বিদায় দিয়েছে। তাতে মানুষের কী
ক্ষতি হয়েছে? তেমনি, ঈশ্বরকেও বিদায় দিলে ক্ষতি কী? ঈশ্বরকে বাদ দিয়েও এ জগতের
সর্বরহস্য ভেদ করা যায়৷ যা দিয়ে তা করা যায় তার নাম বিজ্ঞান।” ধর্মবিশ্বাসে
তিনিও হুমায়ুন আজাদের মতোই ভাবতেন, স্রষ্টার চাইতে মানুষই অধিকতর ক্ষমতাবান!
‘ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা’, ‘ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ’, ‘সংস্কৃতির
সংকট’, ‘পশ্চিম না আধুনিক’ - প্রভৃতি প্রবন্ধে সংস্কৃতি সম্পর্কে অন্নদাশঙ্কর
রায়ের চিন্তার অবয়ব খুঁজে পাওয়া যায়। রেনেসাঁসের প্রভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির বাঁকবদল
এই প্রবন্ধগুলির একটা বড় জায়গাজুড়ে স্থান পেয়েছে।
‘ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা’ প্রবন্ধে তিনি ভারতবর্ষের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের সাংস্কৃতিক অগ্রাযাত্রার আলোচনা শেষে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্য দিয়ে নতুন সংস্কৃতি উদ্ভবের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। “জনগণের দিকে তাকালে আমি অসীম সম্ভাবনা দেখতে পাই। যুগ এখনো অসমাপ্ত। এখন শুধু পশ্চিম ইউরোপ থেকে নয়, পৃথিবীর সব দিক থেকে প্রেরণা আসছে। আমাদের সৃষ্টি বাইরে সম্প্রসারিত হচ্ছে। এর পর আসবে সপ্তম যুগ৷ জনগণের ভিতর থেকে উদ্ভব হবে নতুন সংস্কৃতির।” ভারতীয় সংস্কৃতিতে মুসলিমদের অবদানকে স্বীকৃতি দিয়েছেন অন্নদাশঙ্কর রায়৷ ‘ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ’ প্রবন্ধে অন্নদাশঙ্কর বৈদিক ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি, মুসলিম সংস্কৃতি, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এবং লোকসংস্কৃতিকে একসঙ্গে ‘সংস্কৃতির চতুরঙ্গ’ বলে অভিহিত করেছেন। লোকসংস্কৃতিকে একই সঙ্গে সংস্কৃতির সবচাইতে পুরাতন ও নবীন ধারা বলে উল্লেখ করে এই ধারার অপার সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করেছেন। ‘পশ্চিম না আধুনিক’ প্রবন্ধে যেসব ভারতীয়রা নিজেদের ভাববাদী' আখ্যা দিয়ে আধুনিকতাকে দূরে সরিয়ে রাখেন, তাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন প্রাবন্ধিক। রেনেসাঁসের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে আধুনিকতাকে তিনি ধারণ করতেন এবং ভারতীয়দের মুক্তির একমাত্র পথ ‘চিন্তার আধুনিকতা’ এই চিন্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। ‘পশ্চিম না আধুনিক’ প্রবন্ধে বলেছেন,
“আমাদের দেশ মধ্যযুগে এক পা রেখে আধুনিক যুগে আর এক পা রেখে দুই নৌকায় দোটানায় টাল সামলাতে পারে না, এই অপরূপ সার্কাস তার পক্ষে প্রাণান্তকর।.... মনটা আধুনিক না- হলে আমরা কেবল পরের কাছে পাঠ নিতে থাকব, পরকে শেখাতে পারব না।”
স্বতন্ত্র মানসজগতের অন্নদাশঙ্কর ছিলেন গ্রহণোমুখ ব্যক্তিত্ব।
তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এ দু'ধারা থেকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছেন। সমন্বয় করেছেন।
বলা যায় সমন্বয়বাদী লেখক। সংস্কৃতি ভাবনায় তিনি আধুনিকতা ও ঐতিহ্যকে একসুঁতোয়
বাঁধতে সক্ষম হয়েছিলেন।
অন্নদাশঙ্কর রায় যেমন একদিকে সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক, তেমনই অন্যদিকে মানবিক ও নৈতিক দায়বদ্ধতায় উদার যুক্তিবাদী প্রাবন্ধিক। তিনি জীবনের একপ্রান্তে রস তথা সৌন্দর্যের সাধক, অন্যপ্রান্তে বিবেক তথা সত্যের সৈনিক। তিনি এমন একজন প্রাবন্ধিক ছিলেন, যিনি ক্রমাগত উচ্চতর আদর্শে ও মূল্যবোধে পাঠককে অনুপ্রাণিত করার কাজকে মনে করতেন তাঁর মানবিক কর্তব্য। অন্নদাশঙ্করের প্রবন্ধের রাষ্ট্রভাবনা, ধর্মভাবনা, রাজনীতিভাবনা কিংবা সংস্কৃতিভাবনা আজও শতাব্দী পেড়িয়ে বর্তমানেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। কালকে অতিক্রম করে তিনি কালোত্তীর্ণ হয়েছেন।
বাংলা বিভাগ
উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়










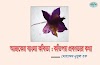








0 Comments