‘বাংলাদেশের উপন্যাসে আঞ্চলিকতা’ এই বিষয়টিকে ভাঙলে অর্থপূর্ণ তিনটি আলাদা আলাদা শব্দ পাওয়া যায়। ‘বাংলাদেশের’, ‘উপন্যাস’ এবং ‘আঞ্চলিকতা’। প্রথম শব্দ দুটির সংযোগ ঘটালে বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, ‘বাংলাদেশের উপন্যাস’ এবং ‘আঞ্চলিকতা’। অর্থাৎ বাংলাদেশের উপন্যাসে বিবৃত আঞ্চলিকতা। তবে তার আগে দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হওয়া দরকার:
ক. বাংলা উপন্যাস এবং
খ. বাংলাদেশের উপন্যাস।
বাংলা উপন্যাসের সূচনাকাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলায় রচিত সকল উপন্যাস অখন্ডভাবে বাংলা উপন্যাসের আওতাধীন। এবং ১৯৪৭ পরবর্তী পূর্ববঙ্গে রচিত উপন্যাসের ধারাটিই হলো ‘বাংলাদেশের উপন্যাস’। অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল পরবর্তী পূর্ববঙ্গে রচিত বাংলাদেশের উপন্যাসে বিধৃত আঞ্চলিকতার উপাদানই আমার আজকের মূল আলোচ্য। বৃহৎ পরিসরে বিষয়টি অনেকাংশে হয়ে উঠেছে ‘বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস’ সম্পর্কিত। এ পর্যায়ে আবারও দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করার প্রয়োজন:
ক. আঞ্চলিক উপন্যাস এবং
খ. উপন্যাসে আঞ্চলিকতা।
একটি বিশেষ ভৌগোলিক পরিসীমা- অন্তর্গত বিশেষ নৃতাত্ত্বিক ঐতিহ্যমণ্ডিত মানবস্প্রদায়ের ভাব-ভাবনা, জীবনাচার অর্থাৎ local color and habitations- এর পূর্ণাঙ্গ শিল্পরূপ হচ্ছে আঞ্চলিক উপন্যাস। আঞ্চলিক উপন্যাসের কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্যও থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারায় এমন অনেক উপন্যাস আছে যেগুলি বৈশিষ্ট্যের বিচারে পুরোপুরি আঞ্চলিক উপন্যাস হয়ে ওঠেনি, কিন্তু আঞ্চলিকতার কিছু উপাদান বিরাজমান, সে উপন্যাসগুলিও আমার নিবন্ধের আলোচিত বিষয়।
উপন্যাস একটি সংস্কৃত শব্দ। উপ-নি-অস+অ(ঘঞ) = উপন্যাস। উপন্যাস শব্দের আক্ষরিক অর্থ ‘কল্পিত কাহিনি’। তবে আধুনিক সাহিত্যে উপন্যাসের অর্থ হচ্ছে- উপস্থাপন। যে বর্ণনাত্মক রচনায় মানুষের বাস্তব জীবনকথা লেখকের জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে উপস্থাপিত হয়, তাকেই উপন্যাস বলে। উপন্যাস হচ্ছে প্রবহমান সময় ও সমাজ অন্তর্গত জীবনের রূপকল্প। উপন্যাসে উপস্থাপিত হয় দেশ-কাল-ইতিহাস-সমাজ-সভ্যতার অন্তর্গত ভাবসত্য। যিনি উপন্যাস রচনা করেন, তাঁকে বলা হয় ‘ঔপন্যাসিক’। স্থির, নিশ্চল-বন্ধ্যা অনুভবে নিজেকে সমর্পণ না করে সৃষ্টিশীল ঔপন্যাসিকগণ মূলত যুগযন্ত্রণা ও যুগবিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তাঁদের সৃষ্টিকর্মে। Anti-plot, anti-hero, anti - time ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে স্থিতপ্রজ্ঞ ঔপন্যাসিকগণ রচনা করেছেন বিভিন্ন শ্রেণির উপন্যাস। যেমন, চৈতন্যপ্রবাহরীতির উপন্যাস, পুরাণাশ্রয়ী উপন্যাস, প্রতীকী বা রূপক উপন্যাস, ঐতিহাসিক- সামাজিক উপন্যাস, দূরায়ত অঞ্চলের জীবনভিত্তিক উপন্যাস প্রভৃতি।
আন্তর্জাতিক সাহিত্যধারায় ‘আঞ্চলিকতা’ একটি প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক ধারণা। যে উপন্যাসে একটি বিশেষ অঞ্চলের ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক ও নির্দিষ্ট জনজাতির আচার-আচরণ, জীবনাচরণ, রীতিনীতি, এককথায় সামগ্রিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়, তাকে বলে আঞ্চলিক উপন্যাস। আঞ্চলিক উপন্যাস লোকজীবন সম্পৃক্ত। লোক জীবনের কৃষ্টি-সংস্কৃতির লিপিবদ্ধ হয় আঞ্চলিক উপন্যাসে। একটি বিশেষ অঞ্চলের মুখের ভাষায় আঞ্চলিক উপন্যাসের ভাষা চয়নের মূলনীতি। সম্ভবত বাংলা উপন্যাসের পরিমণ্ডলে আঞ্চলিক আবহ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম আলোচনার সূত্রপাত করেন প্রখ্যাত গবেষক-সমালোচক ও প্রবন্ধকার শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। আঞ্চলিক উপন্যাস সম্পর্কে তিনি তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে বলেন,
“আঞ্চলিক সাহিত্যে সংজ্ঞানির্দেশ কিছুটা দুরূহ।.....যে সমস্ত প্রত্যন্তস্থিত, ক্ষুদ্র ভূমিখন্ডে ব্যক্তিজীবন গোষ্ঠীজীবনের দ্বারা সম্পূর্ণ কবলিত, যেখানে আদিম যুগোচিত বদ্ধমূল সংস্কার, সমষ্টিগত জীবনাদর্শ ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার নির্মমভাবে কণ্ঠরোধ করিয়াছে, যেখানে ব্যক্তিপরিচয় অপেক্ষা কৌমশাসনই মানবপ্রকৃতির স্বরূপ নির্ণয়ে বেশি শক্তিশালী, কেবল সেইখানে আঞ্চলিক সাহিত্যের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতে পারে।” ১
আঞ্চলিক উপন্যাসের Regionalism সম্পর্কে William Flint Thrall এবং Addison Hibbard তাঁদের ‘A Handbook to Literature' গ্রন্থে যে তথ্য উপস্থাপন করেছেন, তা এখানে প্রণিধানযোগ্য:
"A quality in literature which is the product of its fidelity to a particular geographical section, accurately representing its habits, speech, manners, history, folklore, or beliefs." ২
এই সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে আঞ্চলিক উপন্যাসের কিছু সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। যথা:
★ Particular geographical section (বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চল)
★ Accurately representing its habit (প্রতিবিম্বিত মানুষের জীবনাভ্যাস))
★ Speech (ভাষা)
★ Manners (আচরণ)
★ History (ইতিহাস)
★ Folklore (লোকাচারবিদ্যা)
★ Beliefs (বিশ্বাস)
আঞ্চলিক উপন্যাসের স্বতন্ত্র কিছু মাণদন্ড বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যে বৈশিষ্ট্যেগুলির বিচারে আমরা খুব সহজেই কোনো উপন্যাসের আঞ্চলিকতার উপাদান নির্ধারণ করতে পারি।
ক. নির্দিষ্ট অঞ্চল বা ভৌগোলিকতা:
কোন একটি বিশেষ নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের কথা আঞ্চলিক উপন্যাসের বিবৃত হয়। একটি বিশেষ অঞ্চলের জনসাধারণের ঐতিহ্য, আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি, আদি বিশ্বাস ইত্যাদির পরিচয় থাকে।
খ. সামষ্টিক চরিত্রে প্রতিফলিত নায়কের ভূমিকা:
এ ধরণের উপন্যাসে একটি বিশেষ চরিত্রের প্রাধান্য থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনো একক নায়ক থাকে না। একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাহিনি নায়ক হিসেবে বর্ণিত হয়। অর্থাৎ সামষ্টিক জনগোষ্ঠী নায়কের ভূমিকা পালন করে।
গ. উপন্যাসের ভাষা:
এই উপন্যাসগুলিতে লেখকের দৃষ্টিকোণের বর্ণনা প্রমিত বা সাধু ভাষা হতে পারে। তবে চরিত্রের মুখে আরোপিত ভাষা হয় একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা। একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষের সুখ-দুঃখের ভাষাই আঞ্চলিক উপন্যাসের ভাষা হিসেবে গৃহীত হয়।
ঘ. Local Colar বা স্থানিক রং এবং নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের প্রথা, বিশ্বাস, আচরণ:
এই উপন্যাসগুলিতে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রথা, উৎসব, ঐতিহ্য, ইতিহাসের বিশদ বর্ণনা থাকে। মূলত এগুলির উপর ভিত্তি করেই উপন্যাসের কাহিনি অগ্রসর হয়।
ঙ. দ্বান্দ্বিকতা:
আঞ্চলিক উপন্যাসের মধ্যে একধরণের দ্বন্দ্ব বিরাজমান থাকে৷ উচ্চবর্গের সাথে নিম্নবর্গের দ্বন্দ্ব। অপরদিকে, একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষের উপর অন্য অঞ্চলের মানুষের শাসন-শোষণ ইত্যাদির ছবি তুলে ধরা হয়।
চ. ইতিহাসচেতনা ও প্রকৃতি বর্ণনা:
আঞ্চলিক উপন্যাসগুলিতে যে জনগোষ্ঠী ও অঞ্চলের জীবনাচার উপস্থাপিত হয়, সে অঞ্চল বা জনগোষ্ঠীর একটি সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বর্ণনাও থাকে। এছাড়াও লোকশ্রুতি, কিংবদন্তি ইত্যাদির উপস্থিতি হরহামেশাই পাওয়া যায় এ ধরণের উপন্যাসে। উপন্যাসগুলিতে ভৌগলিক অঞ্চলের প্রকৃতি, কাহিনি ও চরিত্রের পশ্চাৎপট হিসেবে গৃহীত হয়। তবে প্রকৃতি পরিচর্যা এখানে মুখ্য স্থান পায় না।
Local color বা স্থানিক রং আঞ্চলিক উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা হিসেবে বিবেচিত ও স্বীকৃত। Local color এর নিখুঁত উপস্থাপনার মাধ্যমে একটি উপন্যাস আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে সার্থক হয়ে ওঠে। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের দিকে আমেরিকান সাহিত্য জগতে local color পদবন্ধটি বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে৷ সে সময়ে Local color movement নামক একটি সাহিত্য আন্দোলনেরও অস্তিত্ব ছিলো। বিশ্বসাহিত্যের প্রাঙ্গণে বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক আঞ্চলিক উপন্যাস রচনা করেছেন। ইউরোপীয় সাহিত্যের এলিন ব্রন্টির ‘উইদিরিং হাইটস’, জোসেফ কনরাডের ‘দ্য নিগার অফ দ্য নার্সিয়াস’, টমাস হার্ডির ‘ওয়েসেক্স নভেলস’ ইত্যাদি বিখ্যাত আঞ্চলিক উপন্যাস।
বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে সর্বপ্রথম শিল্পসম্মত আঞ্চলিক উপন্যাস রচনায় যিনি পথিকৃতের মর্যাদাপ্রাপ্ত তিনি কল্লোলের কুলবর্ধন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। পদ্মা ও পদ্মাতীরের স্থানিক বর্ণিমার সঙ্গে তৎসন্নিহিত লোকজীবনানুষঙ্গের বিশ্বস্ত রূপায়ণে সমৃদ্ধ তাঁর ‘পদ্মানদীর মাঝি’ (১৯৩৬) উপন্যাসটি৷ বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাসের ধারাটি বহু ঔপন্যাসিকের কলমের আঁচড়ে হয়েছে সমৃদ্ধ। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ (১৯৫১), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’ (১৯৩৬), সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’ (১৯৫৭), মনোজ বসুর ‘বন কেটে বসত’ (১৯৬১), প্রফুল্ল রায়ের ‘পূর্ব পার্বতী’ (১৯৫৭), অদ্বৈত মল্লবর্মণের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ (১৯৫৬), সুবোধ ঘোষের ‘শতকিয়া’ (১৯৫৮) , দেবেশ রায়ের ‘তিস্তা পারের বৃত্তান্ত’ (১৯৮৮), মহাশ্বেতা দেবীর ‘অরণ্যের অধিকার’ (১৯৭৭), অমিয়ভূষণ মজুমদারের ‘মহিষকুড়ার উপকথা’ (১৯৭৮), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আরণ্যক’ (১৯৩৯), সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘ঢোঁড়াই চরিতমানস’ (১৯৪৯,১৯৫১ - প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড)- প্রভৃতি বিখ্যাত বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাস।
বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাসকে অঞ্চল ভিত্তিক কয়েকটি ধারাতে ভাগ করা সম্ভব। যেমন, প্রধান প্রধান নদী-তীরবর্তী অঞ্চল কেন্দ্রিক আঞ্চলিক উপন্যাস, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম-সমুদ্র -উপকূলবর্তী অঞ্চল কেন্দ্রিক উপন্যাস, দক্ষিণ-পূর্ব পাহাড়ি অঞ্চল ও দূরবর্তী সমুদ্রদ্বীপ কেন্দ্রিক আঞ্চলিক উপন্যাস, উত্তর-পূর্ব পাহাড়ি অঞ্চল কেন্দ্রিক আঞ্চলিক উপন্যাস, সাঁওতাল অধ্যুষিত পটভূমির আঞ্চলিক উপন্যাস প্রভৃতি।
বাংলাদেশের বিখ্যাত আঞ্চলিক উপন্যাসগুলো হলো আলাউদ্দিন আল আজাদের ‘কর্ণফুলী’ (১৯৬২), আবু ইসহাকের ‘পদ্মার পলিদ্বীপ’ (১৯৮৬), শামসুদ্দীন আবুল কালামের ‘কাশবনের কন্যা’ (১৯৫৪), ‘জায়জঙ্গল’ (১৯৭৮), ‘সমুদ্র বাসর’ (১৯৮৬), শহীদুল্লা কায়সারের ‘সারেং বৌ’ (১৯৬২), রিজিয়া রহমানের ‘উত্তর পুরুষ’ (১৯৭৭), ‘ধবল জোত্স্না’ (১৯৮১), ‘একাল চিরকাল’ (১৯৮৪), সেলিনা হোসেনের ‘পোকামাকড়ের ঘরবসতি’ (১৯৮৬), ‘সূর্য সবুজ রক্ত’, তাসাদ্দুক হোসেনের ‘মহুয়ার দেশে’, অজয় ভট্টাচার্যের ‘কুলিমেম’, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য৷ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ‘লালসালু’ (১৯৪৮) উপন্যাসটিতে আঞ্চলিকতার কিছু উপাদান থাকলেও তা পুরোপুরি আঞ্চলিক উপন্যাস হয়ে ওঠেনি।
আলাউদ্দিন আল আজাদ রচিত ‘কর্ণফুলী’ (১৯৬২) উপন্যাসটিতে লেখক আঞ্চলিক লােকজীবন ও তার ভাষার পরিচয় দানের চেষ্টা করেছেন। বাইরের জগতের অভিঘাত-সংঘাতে আঞ্চলিক জীবনের রূপের কী ধরণের রূপান্তর ঘটতে পারে তা এখানে দেখানাে হয়েছে। আদিবাসী রাঙামিলা, প্রেমিক দেওয়ানপুত্র (চাকমা), বাঙালি ইসমাইল, জলি, রমজান প্রমুখের জীবনাযাপন ও প্রণয় উপন্যাসটির মূল উপজীব্য। ইসমাইল চোরাকারবারি, উচ্চাভিলাষী। সে আদিবাসী তরুণী রাঙামিলার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ উপন্যাসে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার উপস্থিতি লক্ষনীয়।
স্থানিক বর্ণনা, নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর উল্লেখ এবং ভাষার সমন্বয়ে এটি একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস। ‘সারেং বৌ’ (১৯৬২) উপন্যাসটির কাহিনিমালায় সমুদ্রোপকূলের নাবিকদের জীবন এবং জীবন সংগ্রামের কাহিনি, তাদের বেঁচে থাকার কিংবা খানিকটা আনন্দে জীবন অতিবাহিত করার একটা দাবি বা ইচ্ছার অস্পষ্ট রূপ দেয়া হয়েছে। এই উপন্যাসে স্থানিক প্রেক্ষাপট হিসেবে লেখক বামনছাড়ি গ্রামকে নির্বাচন করেছেন। শহীদুল্লা কায়সার রচিত ‘সারেং বৌ’ উপন্যাসে যে ব্যক্তির গ্রামীণ জীবনের কাহিনি উঠে এসেছে, সে হলো কদম সারেংয়ের বৌ নবিতুনের। নবিতুন বাংলার আপামর হতভাগ্য নারীর প্রতিনিধি হিসেবে এখানে চিত্রায়িত হয়েছেন। যার খসম সাগরদেশে জাহাজের ছোট সারেং এবং সে কিনা প্রতিনিয়ত সংগ্রামের ভেতর দিয়ে নিজের ইজ্জত–আব্রু বাঁচিয়ে একটু একটু চলছেন। কিন্তু মানুষের কামনা দৃষ্টি এবং দীর্ঘ সময় খসম অনুপস্থিতি একজন নারীকে কতটা বিড়ম্বনায় ফেলে বা কাঁটার আঘাত সহ্য করতে হয়, তারই একটা বড় রকমের ইঙ্গিত ‘সারেং বৌ’ উপন্যাসে দেখিয়েছেন শহীদুল্লা কায়সার। ভাষায়ও কোনো জড়তা নেই তেমন, আঞ্চলিক কিছু শব্দ বেশ সাবলীলভাবেই ঢুকে গেলেও কারো বুঝতে বেগ পেতে হয় না। হয়তো ভাষার শক্তি একেই বলে। ‘সারেং বৌ’ বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা বলতে দ্বিধা নেই। যার ভেতর দিয়ে বাংলাদেশকে আরো গভীরভাবে দেখা সহজ হয়। গ্রামজীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস বলতে যা বোঝায় ‘সারেং বৌ’ তেমনই একটা রচনা।
শামসুদ্দীন আবুল কালামের ‘কাশবনের কন্যা’ (১৯৫৪) উপন্যাসে গ্রামকে এমনভাবে তুলে আনা হয়েছে যে, দুঃখ-দারিদ্র্য থাকলেও গ্রামই সুখের স্বর্গ, সমস্ত বিশ্বাসের আধার। উপন্যাসে বরিশাল অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, লােকজীবন, গ্রামীণ দিগন্ত ভাষার ফটোগ্রাফিক আঙ্গিকে চিত্রায়িত হয়েছে। সিকদার, হােসেন, জোবেদা, মেহেরজান প্রমুখের মুখের আঞ্চলিক কথা, লােকসঙ্গীত, প্রচলিত লােকবচন ইত্যাদির ব্যবহার উপন্যাসটিতে local color এর চিত্রায়ণ ঘটিয়েছে।
সেলিনা হোসেনের ‘পোকামাকড়ের ঘরবসতি’ (১৯৮৬) উপন্যাসে আছে নাফ নদীর তীরের জেলেপাড়ার উত্থানের গল্প। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের মাঝিদের জীবন, ভালবাসা, সংসার আর সংগ্রামের গল্পকে ঘিরে বিস্তার পায় ‘পোকামাকড়ের ঘরবসতি’। সেখানে শোষণ আছে, স্বার্থপরতা আছে, হিংসা আছে, হিংস্রতা আছে- কিন্তু এত কিছুর মধ্যেও মানবতা পুরোপুরি বিরাজিত । ‘পোকামাকড়ের ঘরবসতি’ এই মানবতাকে পুঁজি করে কিছু নিপীড়িত মাঝির একত্রিত হওয়ার গল্প, শোষণের জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার গল্প, মাথা তুলে দাঁড়ানোর গল্প।
এই উপন্যাসগুলির মতো অন্যান্য আঞ্চলিক উপন্যাসগুলিও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন্ত ভাষ্য হয়ে উঠেছে, হয়ে উঠেছে তাদের যাপিত জীবনের অনুকাব্যের শিল্পগাঁথা। সাহিত্যে মালো, কাহার, কৃষক, মাঝি প্রভৃতি প্রান্তিক শ্রেণির মানুষদের জীবনকথার প্রতিনিধিত্ব করে আঞ্চলিক উপন্যাসগুলি। বাংলাদেশের কথা সাহিত্যে বিশেষত উপন্যাসে ‘আঞ্চলিকতা’ একটি সমৃদ্ধ শিল্প আঙ্গিক। বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাসের ধারায় বর্ণিত ‘আঞ্চলিকতা’র বিভিন্ন উপাদানগুলি আমাদেরকে আত্মপরিচয় সম্পর্কে আরো সচেতন করে তুলেছে। Particular geographical section, Accurately representing its habit, Speech, Manners, History, Folklore, Beliefs ইত্যাদির সমন্বয়ে বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাসগুলি 'সাহিত্যের' পাশাপাশি ‘স্থানিক ঐতিহাসিক’ মর্যাদাতেও সমাদৃত।
আঞ্চলিক উপন্যাসগুলি বাংলা ও বাংলাদেশের সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পসংযোজন; যার স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়ে চলেছে অঞ্চলনির্ভর মানুষের বৈচিত্র্যবহ বিশ্বস্ত অবয়ব!
তথ্যসূত্র:
১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়/বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা/ মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড-কলকাতা/ ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ/ ১৩৮০/ পৃ.৭৬৩-৭৬৪
২. William Flint & Addision Hibbard/ A Handbook to Literature/The Odyssey Press, New York, U.S.A,/ 1962/ P. 406
ফারজানা অনন্যা
প্রভাষক
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)










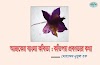








0 Comments