“অন্তর মম বিকশিত
করো / অন্তরতর হে।/নির্মল করো উজ্জ্বল করো,/ সুন্দর করো হে।” রবীন্দ্রনাথের
গানের এই শাশ্বত মঙ্গলময় তিমিরবিনাশী পঙ্ক্তির সৌন্দর্যকে ধারণ করেই যেন প্রতিবছর
সুন্দর ও সত্যের প্রতিষ্ঠার তরে ধরায় আগমন ঘটে বাংলা সনের প্রথম দিনটির। বাংলা
নববর্ষের প্রথম দিন 'পহেলা বৈশাখ' বাঙালির একটি প্রধান সার্বজনীন লোক আনন্দোৎসব । পহেলা বৈশাখ উদ্যাপনের
অন্যতম অনুষঙ্গ মঙ্গল শোভাযাত্রা। যা এ বছর (১৪৩২) ‘বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা’ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। মঙ্গল শোভাযাত্রা আমাদের লোকজ ঐতিহ্যের প্রতীক। মঙ্গল
শোভাযাত্রা অপশক্তির অবসান কামনায় শান্তি যাত্রা। এটি অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে
বাংলাদেশের জনগণের লড়াইয়ে সাহস, শক্তি এবং সত্য ও ন্যায়কে সমর্থন জানানোর
নিদর্শন। বর্ণ, মত, ধর্ম, লিঙ্গ বা বয়স নির্বিশেষে জনগণকে একতাবদ্ধ করার এবং তাদের
গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি সহমর্মিতারও প্রতীক। প্রতি বছরই এই মঙ্গল
শোভাযাত্রার একটি মূলভাব থাকে। সেই মূলভাব প্রতিবাদ এবং দ্রোহের। সেখানে অশুভের
বিনাশ কামনা করা হয়। আহ্বান করা হয় সত্য, সুন্দর এবং মঙ্গলকে। এ বছরের আনন্দ
শোভাযাত্রার প্রতিপাদ্য- ‘নববর্ষের ঐকতান,
ফ্যাসিবাদের অবসান’।
মানুষে মানুষে সম্প্রীতি, নতুনের সূচনা আর অশুভ শক্তির বিনাশে বাঙালির প্রতীকি আয়োজন মঙ্গল শোভাযাত্রা। যেখানে নানান মাসকট, সরাচিত্র, মুখোশ আর মোটিফে তুলে ধরা হয় আবহমান বাংলার লোকজ ঐতিহ্য, অন্যায়ের প্রতিবাদ এবং সত্য-সুন্দর ও মঙ্গলের উদাত্ত আহ্বান। আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য থাকে, মানব জীবনের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি।
মঙ্গল শোভাযাত্রার
বিশ্ব স্বীকৃতি: বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আবেদনের ভিত্তিতে ২০১৬
সালের ৩০ নভেম্বর ‘মঙ্গল শোভাযাত্রা’ জাতিসংঘের সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোর
সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান পায়। ইউনেস্কো মঙ্গল শোভাযাত্রাকে তাদের
‘রিপ্রেজেনটেটিভ লিস্ট অব ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটি’র তালিকায়
অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। সে সময় স্বীকৃতি দেওয়ার কারণ হিসেবে তারা উল্লেখ করে, এটা
শুধু একটা সম্প্রদায় বিশেষের নয়, গোটা দেশের মানুষের, সারা পৃথিবীর মানুষের। আর
এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে মঙ্গল শোভাযাত্রায় যোগ হয় বিশেষ মাত্রা। বাঙালি
সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বব্যাপী, হয়ে ওঠে বিশ্ব সংস্কৃতির অংশ।
বাঙালির পহেলা বৈশাখ উদ্যাপনের ইতিহাস কয়েকশ বছরের পুরনো হলেও মঙ্গল শোভাযাত্রার ইতিহাস খুব বেশি পুরনো নয়। মঙ্গল শোভাযাত্রা প্রথম শুরু হয়েছিল ১৯৮৫ সালের পহেলা বৈশাখে যশোরে। তখন দেশে ছিল সামরিক শাসন। উদ্দেশ্য ছিল দেশের লোকজ সংস্কৃতি উপস্থাপনের মাধ্যমে সব মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা। আর সেই শোভাযাত্রায় অশুভের বিনাশ কামনা করে শুভশক্তির আগমনের প্রার্থনা করা হয়। এর উদ্যোগ নিয়েছিলেন চারুশিল্পী মাহবুব জামাল শামিম।১৯৮৯ সালে পহেলা বৈশাখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা থেকেও শুরু হয় এই মঙ্গল শোভাযাত্রা। শুরুতে এর নাম ‘আনন্দ শোভাযাত্রা’ ছিল। সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থাকে মাথায় রেখেই এমনটা করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এটি 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' হিসেবেই পরিচিত হয়।
মঙ্গল শোভাযাত্রায় যেসব প্রাণী ও বিষয়ের মোটিভ ব্যবহার করা হয় সেসবের অধিকাংশই বাংলার আবহমান কৃষিভিত্তিক সমাজ, রাজনীতি এবং লোকসংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে প্রদর্শিত হয়।
মঙ্গল শোভাযাত্রায় সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় বাংলার আবহমান কৃষিভিত্তিক সমাজজীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিভিন্ন মোটিভ। ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের 'পেঁচা' মঙ্গলযাত্রার একটি পরিচিত পাখি। আবার পেঁচা কৃষকের বন্ধু পাখি। তারা ইঁদুর খেয়ে কৃষকের ফসল রক্ষায় সাহায্য করে। কৃষকের বন্ধু হিসেবে, মঙ্গলের প্রতীক হিসেবে পেঁচা প্রদর্শিত হয় মঙ্গল শোভাযাত্রায়। মঙ্গল শোভাযাত্রায় প্রায়ই ব্যবহৃত হয় 'মাথাল'। বাঁশ, বেতের তৈরী মাথাল মাথায় পরে কৃষকরা চাষের সময় নিজের রোদবৃষ্টি থেকে রক্ষা করেন। ১৪৩২ বঙ্গাব্দের মঙ্গল শোভাযাত্রায় 'লাঙ্গল' একটি গুরুত্বপূর্ণ মোটিভ হিসেবে স্থান পেয়েছে। লাঙ্গল কৃষিভিত্তিক সমাজের আদি উপকরণ। ফসল বোনার জন্য মাটি প্রস্তুতকরণের প্রধান যন্ত্র। এছাড়াও কুলা, পলো, মাছের চাই এবং মাছের ডোলাও প্রায়শই থাকে মঙ্গল শোভাযাত্রায় বিভিন্ন রূপে। ১৪৩২ বঙ্গাব্দের মঙ্গল শোভাযাত্রা ছাড়াও 'ষাড়' ও 'মহিষ' বারবারই বিভিন্ন বছর শোভাযাত্রায় প্রাণীর মোটিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। 'ষাড়' ও 'মহিষ' কৃষিভিত্তিক সমাজে লাঙল চালানোর প্রাণী হিসেবে যেমন ব্যবহৃত হয় আবার গবাদিপশু হিসেবেও এদের কদর অত্যধিক। তবে মাঝে মাঝে এ প্রাণী দুটি কৃষিভিত্তিক সমাজের প্রতীক ছাড়াও বাঙালির বিদ্রোহ সত্তার প্রতীক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।
মঙ্গল শোভাযাত্রার সূচনাই হয়েছিলো রাজনৈতিক বন্দিদশার প্রেক্ষিতে। তখন ১৯৮৫ সাল। সাম্প্রদায়িক সামরিক শাসনের রোষানলে রাজনৈতিক অঙ্গনে তখন ঘোর অমানিশা। শিল্প-সংস্কৃতির অঙ্গনেও মুমূর্ষু দশা। এই বন্দিদশায় একটুখানি ‘খোলা হাওয়া’ পাওয়ার আশায় চারুপীঠের কর্মীরা এমন একটা অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক আয়োজনের পরিকল্পনা করল, যা দিয়ে দেশের নিজস্ব সব শিল্পকে একসঙ্গে মেলানো যাবে এবং সবার প্রাণকে একই সুরে বাঁধা যাবে। এই ভাবনা থেকে সে বছর একুশে ফেব্রুয়ারিতে প্রভাতফেরির পর যশোরের রাজপথে বের করা হলো বর্ণিল ও সুসজ্জিত এক শোভাযাত্রা। ১৪১৮ সালের নববর্ষে বের করা হয় বিশাল আকৃতির একটি কদাকার কুমির। এই কুমিরটি প্রদর্শিত হয়েছিলো মুক্তিযুদ্ধে রাজাকারের প্রতীক হিসেবে। কুৎসিত কুমিরটার মতো রাজাকাররাও ছিলো মানুষখেকো। তারা হত্যা করেছে অসংখ্য মানুষ। বিশ্রী সেই কুমিরটাকে তাই একজন বাঙালি পুরুষ ও একজন বাঙালি নারীর পায়ের নিচে দেখানো হয়েছিলো। ১৪২০ সনে বাঁশ, বেত ও কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়েছিলো বিরাট একটি কদাকার সরীসৃপ। অনেকটা ড্রাগনের মতো দেখতে। রাজাকারদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ফুটিয়ে তোলার জন্য এই ড্রাগন সদৃশ সরীসৃপটি প্রদর্শিত হয়েছিলো। ১৪৩২ মঙ্গল শোভাযাত্রায় জুলাই বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে ফ্যাসিবাদী শাসনের চিত্র তুলে ধরতে ‘ফ্যাসিবাদের মুখাকৃতি’ মোটিফ রাখা হয়েছে। শোভাযাত্রায় স্থান পেয়েছে মুগ্ধের প্রতীকী পানির বোতল। এটি দ্বারা জুলাই গণঅভ্যুত্থানে জীবন দেওয়া শহিদদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ১৯৪৭,১৯৫২, ১৯৭১ এর রাজনৈতিক ঘটনাবলি বারবার বিভিন্ন মঙ্গল শোভাযাত্রায় বিভিন্নরূপে প্রদর্শিত হয়েছে। জাতীয় রাজনীতিকে ছাড়িয়ে এবার শোভাযাত্রায় উঠে এসেছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রসঙ্গ। এ বছর ফিলিস্তিনের নিপীড়িত মানুষের লড়াই সংগ্রামের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে 'তরমুজের ফালি' মোটিফ হিসেবে রাখা হয়েছে। তরমুজ ফিলিস্তিনিদের কাছে প্রতিরোধ ও অধ্যাবসায়ের প্রতীক হিসেবে পরিচিত।
ঘোড়া, বাঘ, দোয়েল, হাতি, ময়ূর, শান্তির পায়রা, নীলগাই, ভেড়া, কাকাতুয়া প্রভৃতি বাংলার জীববৈচিত্র্যের অংশ এবং বাঙালির শাশ্বত সুন্দরের প্রতীকায়ত পশু-পাখি হিসেবে প্রদর্শিত হয়। যদিও ১৪১৮ বঙ্গাব্দে প্রদর্শিত কাকাতুয়া পাখিটি দেশীয় পাখি নয়। শাশ্বত সুন্দরের প্রতীক হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছিলো পাখিটি। বাঙালির খাদ্যাভাস হিসেবে থাকে ইলিশ মাছ, কাঁঠাল, তাল, পেয়ারা প্রভৃতি।
পাখা, বেহুলা, বনবিবি, মুখোশ, পটচিত্র, নাগরদোলা, চরকি, তালপাতার সেপাই, ঢোল, করতাল, নকশিকাঁথা, রিকশা, আলপনা, টেপাপুতুল (মা ও শিশু), রাজা-রানির মুখবয়াব প্রভৃতির মোটিফ বাঙালির লোকসংস্কৃতির জীবনঘনিষ্ঠ প্রতিবিম্ব। 'বেহুলা' কেবল মনসামঙ্গল কাব্যের একটি নারী চরিত্র নয়; বরং বাঙালি নারীর শাশ্বত সংগ্রাম ও সংর্বসহা রূপের প্রতীক। টেপাপুতুলে কখনো ফুটে ওঠে নারীর রূপময়তা, আবার কখনো স্নেহবাৎসল্যতা। নকশিকাঁথা, আলপনা, পটচিত্র বাঙালির শিল্পিত সৌন্দর্যবোধের প্রতীক। যা জাতীয় প্রাঙ্গন ছাড়িয়ে সমগ্র বিশ্বে আজ সমাদৃত। ঢোল, করতাল, তবলা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাঙালির সংগীত সাধনাকে নির্দেশ করে। বনবিবি বাঙালির আরণ্যক জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে। রাজা-রানীর মুখবয়াব বাঙালির লোককাহিনিকে নির্দেশ করার পাশাপাশি বাঙালি নর-নারীর দাম্পত্য সম্প্রীতিরও প্রতীক। তালপাতার সেপাই বাঙালির শিশুর খেলনাসামগ্রী। যা শিশুকে শক্তিশালী হতে অনুপ্রাণিত করে। চরকি নাগরদোলা বাঙালি শিশু বিনোদনের সামগ্রী। এরকম প্রতিটি মোটিভ বাঙালির আদি জনজীবনকে স্মরণ করায়। শিকড়কে মনে রেখে মাটির দিকে সংযোগ সাধন করে।
আনন্দ শোভাযাত্রা কিংবা মঙ্গল শোভাযাত্রা এখন বাঙালির জাতীয় অঙ্গনকে ছাড়িয়ে পেয়েছে আন্তর্জাতিক মাত্রা। বাঙালির নিরলস নিঃসংশয় যাত্রার অফুরান শক্তিকে জাগ্রত করে সুন্দরের দিকে চোখ রাখার প্রত্যয়েই এই শোভাযাত্রার উদ্ভব। মঙ্গল শোভাযাত্রা বাঙালির অর্থনীতির আদি শেকড় 'কৃষি', রাষ্ট্র চালিকাশক্তির মতাদর্শ 'রাজনীতি' এবং আত্মপরিচয়ের প্রতিবিম্ব 'সংস্কৃতি'কে একসাথে যুক্ত করে বাঙালির মননকে মুক্ত করে অপসংস্কৃতির ছায়া থেকে। নির্ভীক বাঙালির এই শোভাযাত্রা আনন্দের, গৌরবের, সুন্দরের যাত্রা! এই যাত্রা বাঙালির জীবন থেকে অপশক্তিকে বিনাশ করার যাত্রা!
লেখক -
প্রভাষক
বাংলা বিভাগ
উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়










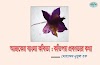








0 Comments